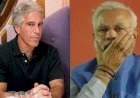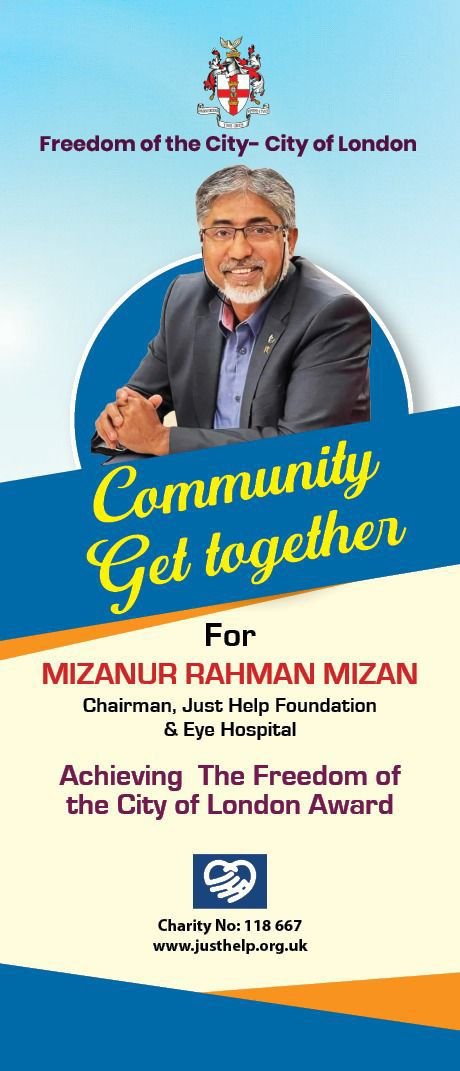পিআর পদ্ধতির পক্ষে আছি, পক্ষে নাই

আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী:
পক্ষে আছি, পক্ষে নাই। বুঝি না, কিছু বুঝিয়ে দিন। সারাদেশে এই রব পিআর নিয়ে। ‘পিআর’ ইংরেজি সংক্ষেপ, যার মূল শব্দ হচ্ছে প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। বিষয়টি আসলে কী?
উদাহরণ হিসেবে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের বিপরীতে ৪২৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৭৫টি রাজনৈতিক দল থেকে মোট দুই হাজার ৭৮৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনজন স্বতন্ত্র সদস্যসহ ১২টি দলের প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হন। দেশে এ যাবৎকালের সর্বাধিক স্বচ্ছ নির্বাচন বলে পরিচিত সেই নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৫.৪৫ শতাংশ। নির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি যথাক্রমে কাস্টিং ভোটের ৩০.৮১, ৩০.০৮, ১২.১৩ ও ১১.৯২ শতাংশ পেলেও আসন পায় যথাক্রমে ১৪০, ৮৮, ১৮ ও ৩৫টি। একই নির্বাচনে জাকের পার্টি ১.২২ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১.১৯ শতাংশ ভোট পেলেও আসন বিচারে আসন লাভ করে যথাক্রমে ০ ও ৫টি।
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে ওই নির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি যথাক্রমে ৯২, ৯০, ৩৬ ও ৩৬টি আসন লাভ করত। আসনভিত্তিক নির্বাচনে জাকের পার্টি একটি আসনের দখল না পেলেও পিআর পদ্ধতিতে চারটি আসন জুটে যেত। জাকের পার্টিসহ আরও আটটি দল, যারা সংসদে আসন পায়নি, তারাও আসন লাভ করত। এ কারণেই সারাদেশে বিস্তার আছে কিন্তু এককভাবে কোনো আসনে ব্যাপক জনসমর্থন নেই– এমন দলগুলো পিআর পদ্ধতির পক্ষে সোচ্চার হয়েছে।
পৃথিবীর ১৩০টিরও বেশি দেশে পিআর পদ্ধতি চালু আছে। তবে যে দেশগুলোর গণতন্ত্রকে আমরা অনুসরণের চেষ্টা করি, যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ভারত পিআর পদ্ধতির আশ্রয়ে যায়নি। রাজা শাসিত বা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের দেশগুলোর বাইরে সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকার পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ও ইসরায়েল পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করে।
পিআর পদ্ধতিতে এককভাবে কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা কম, ফলে সরকার স্বৈরাচারী হওয়া দূরের কথা, স্থায়িত্বই পায় না। সে কারণেই ২০০৮ সালে নেপালের রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর গত ১৭ বছরে আটজন ব্যক্তি মাত্র ১৩ বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ইসরায়েলের মতো ফিলিস্তিনেও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। ফিলিস্তিনে পিআর পদ্ধতি কেন সে বিষয়ে বাস্তব উদাহরণ হিসেবে কল্পনা করা যায় রোহিঙ্গা পরিস্থিতি। ধরা যাক রোহিঙ্গা শরণার্থীরা স্বাধীন রাষ্ট্র করার কথা ভাবল, তবে তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে কীভাবে? তাদের যে শরণার্থী দশা, তাতে করে সংসদের সদস্য যত সংখ্যকই হোক, আসনভিত্তিক নির্বাচন করা দুরূহ। সে ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের অধিবাসীদের জন্য পিআর পদ্ধতিই হবে শ্রেয়। একই কারণে ফিলিস্তিনে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। নেপালের পিআর পদ্ধতির নির্বাচন মিশ্রভাবে হয়ে থাকে। ২৭৫ আসনের ১৬৫টি আসন সংসদীয় আসনভিত্তিক নির্বাচন এবং বাকি ১১০টি প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে। সেখানেও কিন্তু আছে; ৩ শতাংশের কম প্রাপ্ত ভোট আসন ভাগের জন্য বিবেচনায় আনা হয় না।
পিআর পদ্ধতির ভালো দিক হলো, এ পদ্ধতিতে কোনো দলেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার ফলে স্বৈরাচারী সরকার আসার কোনো কারণ থাকবে না। আসনভিত্তিক নির্বাচনে ভোটারের একটি এলাকা থাকে, সেই এলাকায় প্রার্থী থাকেন। ভোটার কেবল পার্টি বিবেচনা করে ভোট দেন না, প্রার্থীর গুণমানও বিচার করেন। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে যেহেতু কোনো প্রার্থী থাকবে না, সে কারণে ভোটারের প্রার্থী বাছাইয়ের কোনো আবেগ কাজ করবে না। আবেগবিহীন নির্বাচনে শুধু পার্টিজানরাই ভোট দিতে আগ্রহী হবেন এবং সে কারণে কখনও কোনো দল এককভাবে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পাবে না, সে গ্যারান্টি দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। আলোচনা হচ্ছে, প্রার্থী মনোনয়নের সময় কোনো কোনো রাজনৈতিক দল প্রচুর টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন দিয়ে থাকে। পিআর পদ্ধতিতে যেহেতু মনোনয়ন থাকবে না, তাই মনোনয়ন বাণিজ্যও হবে না।
শুনতে ভালো লাগলেও মনে প্রশ্ন জাগে, পিআর পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দল যে ক্রমতালিকা করবে, তাতে কোনো বাণিজ্য হবে না– তা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে? প্রচলিত পদ্ধতিতে নূর মোহাম্মদ মণ্ডলের মতো একজন স্থানীয় নেতা শেখ হাসিনাকে পরাজিত করে জাতীয় সংসদের সদস্য হতে পারেন, কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে তিনি দলের ৩০০ শীর্ষ নেতার তালিকায় নাম ঢোকাতে পারতেন কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ থাকবে। কোনো প্রার্থী মনোনয়ন বাণিজ্য করে মনোনয়ন কিনলে তাতে ভোটারের কোনো উনিশ-বিশ হয় না। মনোনয়ন বাণিজ্যে হেরে যাওয়া ব্যক্তিও নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হওয়ার প্রচুর উদাহরণ আছে। অথচ পিআর পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের অনুগ্রহ ছাড়া সংসদ সদস্য হতে পারবেন না।
সারাদেশে দলের তেমন বিস্তার না থাকলেও কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় ব্যক্তিবিশেষ নিজস্ব ভাবমূর্তির কারণে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এমনকি প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও গোয়ালন্দ থেকে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন, পরেও তেমন ঘটনা অনেক আছে। এমনকি সর্বশেষ ডামি নির্বাচনেও দু’জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ক্ষমতাসীন দুই মন্ত্রীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ পিআর পদ্ধতির নির্বাচন হলে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচন করার কোনো সুযোগই থাকবে না।
তবে হ্যাঁ, আসনভিত্তিক নির্বাচনে সব আসনে কোনো দলের প্রার্থীরা জামানত হারালেও সারাদেশে প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে সংসদে এক বা একাধিক প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ পাবে। এই সুযোগ নিতে কোনো সমাজে ধিকৃত কোনো পেশার মানুষ একত্র হয়ে একটি দল গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও করতে পারে। যেহেতু ভোটারের সামনে কোনো প্রার্থীকে দাঁড় করাতে হবে না, তাই কোনো দ্বিধাও কাজ করবে না। সেই দল যদি দেশের ৪২ হাজার ৫০০ কেন্দ্রের প্রতিটিতে গড়ে ১০টি করেও ভোট পায় তাহলে মোট ভোট হবে ৪ লাখ ২৫ হাজার। বর্তমান ভোটার সংখ্যার ৬০ শতাংশ ভোট কাস্ট হলেও সেই দল ৩০০ আসনের সংসদে একটি আর ৪০০ আসনের সংসদে দুটি আসন পেয়ে যাবে। ভালো দলের প্রতিনিধি আসার যেমন সম্ভাবনা তৈরি হবে, তেমনি তৈরি হবে মন্দ লোকদেরও সংসদে আসার।
সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ থাকুক বা না থাকুক, পিআর পদ্ধতিতে গুটি গুটি আসনপ্রাপ্তরা হয়ে উঠবেন সরকারের স্থায়িত্বসহ বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান নিয়ামক। তখন যদি সেই সব সদস্য আজ একে কাল ওকে সমর্থন করেন, সেটা হবে তাদের স্বাধীনতা। শুধু দেশের পুঁজি বিনিয়োগকারীরা নন, বিদেশেরও অনেকে নিজ নিজ স্বার্থে বাজি ধরবেন এসব সদস্যের ওপর। তখন সাধারণ মানুষ হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে, আহা!
আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী: কলাম লেখক; অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব